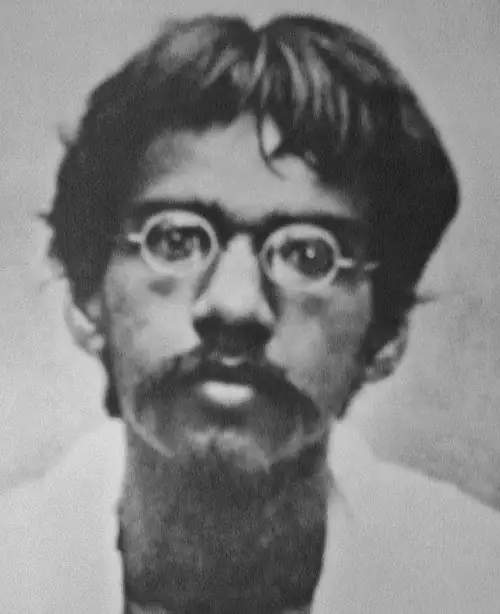প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের ক্রমবিকাশ, উপভাষাগত অনুবর্তন, এবং সাহিত্যিক নিদর্শনের অনুবৃত্তি
কালিদাসকৃত বিক্রমোর্বশীয়ম্ (চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী খ্রি) নাটকে অপভ্রংশ ভাষার ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়, বিশেষতঃ স্ত্রীপাত্র ও বিদূষকচরিত্রের মুখে। এই ব্যবহার একদিকে নাট্যশাস্ত্রীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিলেও, অপরদিকে তৎকালীন জনভাষার প্রতিফলনও বহন করিত। এই অপভ্রংশরূপী ভাষাগুলি, যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম হইতে বিচ্যুত, প্রকৃতপক্ষে সেই ভাষারই বিকৃত বা প্রচলিত রূপ, যাহা সাধারণ জনমানসে কথিত হইত।
প্রাচীন কামরূপ (পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী) অঞ্চলে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিল, যাহা ‘গৌড়-কামরূপী প্রাকৃত’ হইতে উদ্ভূত। অনেক পণ্ডিতের অভিমত—মাগধী অপভ্রংশ হইতেই অসমীয়া, বাঙলা ও ওড়িয়া এই তিনটি নিকটাত্মীয় ভাষার উদ্ভব হইয়াছে, যাহার ফলে এই ভাষাসমূহের মধ্যে স্বরূপগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। সংস্কৃতশব্দ ‘অপভ্রংশ’র আক্ষরিক অর্থই ‘ভ্রষ্ট’ বা ‘ব্যাকরণবিরুদ্ধ ভাষা’। যেখানে সংস্কৃত ছিল বিশুদ্ধ, বিধিবদ্ধ, পাণ্ডিত্যসাধিত ভাষা, সেখানে প্রাকৃত ছিল প্রাকৃতিক বা দেশজ রীতি অনুযায়ী কথিত, এবং সাধারণের ভাষা বলিয়া গণ্য হইত।
ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ও জৈন প্রবর্তকগণ প্রাকৃত ভাষাকে শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মপ্রচারের জন্য গ্রহণ করেন, ফলে এই ভাষার মান ও ব্যাপ্তি দুইই বৃদ্ধি পায়। পালি, যাহা মূলত মাগধী প্রাকৃতের সমন্বয়ে গঠিত, বৌদ্ধধর্মের প্রথম ভাষা এবং ‘ত্রিপিটক’ নামক শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থসমূহ এই ভাষায় লিখিত। প্রখ্যাত রুম্মিনদেই স্তম্ভলিপিতে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী) যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে—”देवाःनंपियेन पियदसिन लाजिना…”—তাহা প্রাকৃত ভাষার এক প্রাচীন নিদর্শন।
মথুরা, যাহা শৌরসেন রাজ্যের রাজধানী (খ্রিস্টপূর্ব ৭ম শতাব্দী) ছিল, সেখানকার প্রাকৃত ‘শৌরসেনী’ নামে খ্যাত। এই শৌরসেনী হইতেই খড়িবোলি, ব্রজ, আওধি প্রভৃতি পশ্চিম হিন্দি উপভাষাগুলির উৎপত্তি। গহড়বাল রাজসভার কবি নয়চন্দ্র রচিত ‘রম্ভামঞ্জরী’ শৌরসেনী প্রাকৃত ভাষায় রচিত। অপরদিকে, পূর্বভারতে পালরাজারা (৭৫০-১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ)‘অবহট্ট’ ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যাহা উত্তর ভারতের অপভ্রংশ হইতে ওড়িয়া, বাংলা, অসমীয়া, বিহারী প্রভৃতি ভাষার অগ্রপথ নির্মাণ করিয়াছে।
প্রাকৃত ভাষা প্রকৃতপক্ষে কোনো একক ভাষা নহে, বরং বিভিন্ন জনপদীয় উপভাষার সমাহার, যাহারা এক প্রাচীন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃত ভাষাগুলি, যদিও কথ্যরূপে প্রচলিত ছিল, তথাপি শিলালিপি, ধর্মগ্রন্থ ও নাট্যপাঠে সংস্কৃত ভাষার সহিত সমভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদান্ত যেহেতু সংস্কৃত রক্ষা করিয়াছে, সেই সময়ে শ্রমণদর্শনের প্রবর্তকগণ (খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক নাগাদ) প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ প্রদান আরম্ভ করেন।
‘প্রাকৃত’ শব্দটি অনেকসময় ‘প্রাকৃতিক’ অর্থে গৃহীত হইলেও প্রকৃতার্থে তাহা ‘গ্রাম্য’ বা ‘অপভ্রষ্ট’ ভাষা নির্দেশ করে। ভারতমুনির নাট্যশাস্ত্রে (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চশ শতকের পূর্বে রচিত) ভাষার শ্রেণীবিন্যাসের উল্লেখ আছে—যেমন ‘অতিভাষা’ (দেবভাষা), ‘আর্যভাষা’ (অভিজনের ভাষা), ‘জাতিভাষা’ (সাধারণ মানুষের ভাষা), ‘যোন্যন্ত্রিভাষা’ (অরণ্য ও গ্রামবাসীদের ভাষা) এবং ম্লেচ্ছভাষা। নাট্যশাস্ত্র অনুসারে, জাতিভাষার দুইরূপ—সংস্কৃত (সুশ্রুত ভাষা) ও প্রাকৃত (স্বাভাবিক বা অপরিশীলিত ভাষা)।
এই ব্যাকরণগত রূপান্তরপ্রবণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ—সংস্কৃত ‘आर्य/आर्ये’ অপভ্রংশে ‘अज्ज/अज्जे’ এবং পরে ‘জী’, ‘जी’ হইয়াছে। সংস্কৃত ‘अस्मि’ অপভ্রংশে ‘ह्मि’ হইয়াছে, যাহা হিন্দীতে ‘हूँ’। এই ধরণের শব্দরূপান্তর নাট্যগ্রন্থ ও শিলালিপিতে বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, মৃচ্ছকটিকম্ নাটকে সূত্রধার ও নটীর কথোপকথনে এইরূপ প্রাকৃত রূপের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
একইভাবে, মুসলিম কবি আব্দুর রহমান (দ্বাদশ শতাব্দী), যিনি কালিদাসকৃত মেঘদূত হইতে অনুপ্রাণিত হইয়া সন্দেশরাসক নামক কাব্য রচনা করেন, অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত একমাত্র মুসলিম কাব্যরচয়িতা বলিয়া খ্যাত।
সেখানে তিনি বলেন—
“माणुस्सदुव्वविज्जाहरेहिं णहमग्गि सूर ससि बिंबे।
आएहिं जो णमिज्जइ तं णयरे णमह कत्तारं॥”
—অর্থাৎ, “হে নাগরিকগণ! যাহাকে মানুষ, দেবতা, বিদ্যাধর, সূর্য ও চন্দ্র নমস্কার করেন, তোমরা সেই সৃষ্টিকর্তাকে নমস্কার কর।”
প্রাকৃত ভাষা আদতে একক কোনো ভাষা নহে, বরং একবিংশতিতম ভাষার সমষ্টিবাচক নাম, যাহারা মূল সংস্কৃত ভাষার ভ্রষ্ট বা প্রচলিত রূপস্বরূপ বিকশিত হইয়াছিল। এই ভাষাগুলি নানা জনপদে, নানা লৌকিক প্রভাবে, স্থানীয় অনুষঙ্গযোগে বিকৃত হইয়া পরবর্তীকালে অপভ্রংশ নামে পরিচিত হইয়াছে। বিশেষত ইসলাম আগমনের পর, এই প্রাকৃত-ভাষাসমূহ অধিকতর বহিরাগত শব্দ ও ধ্বনি প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে।
প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা ও তাহার অপভ্রংশ রূপগুলির তুলনামূলক তালিকা নিম্নরূপ:
- মাহারাষ্ট্রী → মারাঠি
- দক্ষিণাত্য → কন্নড়, তেলুগু, তুলু
- পৈশাচী → পাঞ্জাবি, লাহান্ডা, সারাইকি
- ব্রাচড় → সিন্ধি
- শৌরসেনী → গুজরাটি, পাহাড়ী, ব্রজ, কান্নৌজি, বুন্দেলি
- অর্ধমাগধী → আওধি, বাঘেলি, ছত্তিশগঢ়ি
- মাগধী / পালি → মৈথিলি, ওড়িয়া, বাংলা
- প্রাচ্য → অসমীয়া, মণিপুরি
- অবন্তিকী → মালবী
- আভীরী → রাজস্থানি
- দার্দী → কাশ্মীরি
ইহার অতিরিক্ত ছিল—গান্ধারী, বাহ্লিক, সহকারী, শাবরী ইত্যাদি ভাষা।
‘সংস্কৃত’ শব্দের ব্যুৎপত্তি হইল “সম্ + কৃত” অর্থাৎ ‘সম্যক্ কৃত’—যাহা বিশুদ্ধ রূপে নির্মিত; অপরদিকে ‘প্রাকৃত’ শব্দের অর্থ ‘প্রাকৃতিক’ বা ‘গ্রাম্য’ অথচ আক্ষরিকভাবে “প্র + কৃত” অর্থাৎ ‘কৃত্রিম’ বা ‘অপ্রসিদ্ধ’ রূপ। অতএব, প্রাকৃত ভাষাগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণনির্দিষ্ট বিধি হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহারই লৌকিক ও প্রচলিত রূপে গৃহীত হয়।
এই ভাষাসমূহের বিকাশ ও বিকৃতি সম্বন্ধে শক্ত প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন পালী ভাষায়—
गहपति कुद्दालेन भूमियं कूपं खणिस्सति
(গহপতি কু্দ্দালেন ভূমিয়ং কূপং খণিস্সতি)
এর সংস্কৃত রূপ— गृहपति कुद्दालेन भूम्यां कूपं खनिष्यति।
আবার, প্রাকৃত কাব্য গাথা সপ্তশতী-র (Gāhā Sattasai) একটি শ্লোক—
जो सीसम्मि विइण्णो मज्झ जुआणेहिं गणवइ आसी।
तं व्विअ एह्णिं पणमामि हइजरे होहि संतुट्ठा॥
ইহার সংস্কৃত রূপ—
यः शीर्षे वितीर्णो मम युवभिर् गणपतिर् आसीत्।
तं एव इदानीं प्रणमामि हतजरे भव संतुष्टा॥
উপরন্তু, শকুন্তলা নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত সংলাপ— ण केवलं ताद-निओओ त्ति। बहु-माणो जाव मम अवि। सोदरी-सिणेहो एदेसु अत्थि य्येव।
এর সংস্কৃত রূপ— न केवलं तात-नियोग इति। बहु-मानो यावन् मम अपि। सहोदरी-स्नेह एतेषु अस्ति एव।
এইখানে লক্ষণীয় যে, সংস্কৃত ধাতুগত শব্দ যেমন “मत”, “मद”, “मय”, “मृग”, “मृत”—এই সকল শব্দ প্রাকৃতে “মঅ” হইয়া গিয়াছে; এবং বাংলার “খোকা”, “খুকি”, “কুড়ি”, “ঝোল”, “ঝিনুক” প্রভৃতি শব্দ মুণ্ডা/কোল ভাষা হইতে গৃহীত, যাহা অপভ্রংশ ভাষাসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া পরে আঞ্চলিক ভাষায় স্থায়ী হইয়াছে।
অর্ধমাগধী, জৈন ক্যাননের ভাষা, সকল প্রাকৃতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বা ‘শিষ্ট’ বলিয়া গণ্য। নাট্যশাস্ত্রের বিধানানুসারে, শিক্ষিত চরিত্রগণ সংস্কৃত ভাষায়, সাধারণ চরিত্রগণ মাগধী প্রাকৃতে, এবং অশিক্ষিত বা হাস্যরসাত্মক চরিত্রগণ শৌরসেনী ভাষায় বাক্প্রয়োগ করিত। পালি, মাগধী প্রাকৃতের একটি শুদ্ধ রূপ, প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের মূল ভাষা।
একটি উপমা—
সংস্কৃত (Sanskrit): যদ্ আর্য আজ্ঞাপয়তি (অর্থ: যাহা আর্য আদেশ করেন।)
মাগধী প্রাকৃত (Magadhi Prakrit): জম্ অজ্জো আণৱেদিত্তি (অর্থ: যাহা অজ্জ (আর্য) আদেশ করেন।)
এই তুলনা হইতে স্পষ্ট হয়, “আর্জ্য/আর্য” শব্দটি মাগধীতে রূপান্তরিত হইয়াছে “অজ্জ” আকারে; আর “আজ্ঞা” (ājñā) হইতে “আণৱেদি” বা “আণৱেদিত্তি” হয়েছে, যাহা অধিকতর কথ্য ও সরলরূপ। এইখানে ‘आर्य’ → ‘अज्ज’, এবং ‘आज्ञा’ → ‘आणवेदि’ ইত্যাদি রূপান্তর ভাষাবিকাশের প্রমাণ।
প্রাকৃত কাব্য গাথা সপ্তশতী (মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত): গাথাসপ্তশতীর প্রণয়পূর্ণ কাব্যশ্লোকাবলীতে, যাহা সংস্কৃত সাহিত্যের সংবেদনশীল প্রতিচ্ছবি বহন করে, প্রাকৃত ভাষার রমণীয় কাব্যরূপ দেখা যায়।
জঈ সো ণ বল্লহো ব্বিঅ গোত্ত-গ্গহণেণ তস্স সহি কীস।
হোই মুখং তে রবি-অর-ফংস ব্বিসদং ব তামরসং॥ ৩৪৩
হে বান্ধবী! যদি সে ব্যক্তি তোমার প্রিয় না হয়, তবে কেবলমাত্র তাহার নাম উচ্চারণে, তাহার গোত্র স্মরণে, কিঞ্চিৎ তাহার নামক বন্ধুদের কথা শোনামাত্রই, তোমার মুখমণ্ডল কীভাবে সূর্যকিরণের স্পর্শে বিকশিত পদ্মসম দীপ্ত হইয়া উঠে?
মাণ-দুম-পরুস-পবণস্স মামি সৱ্বঙ্ ণিব্বুই অরস্স।
অৱঊহণস্স ভদ্দং রই ণা়ডঅ পুব্বরঙ্গস্স॥ ৩৪৪
হে খুড়িমাতা! বরং বর হউক সেই আলিঙ্গন, যাহা প্রবল পবনের ন্যায় রোষের বৃক্ষকে ভেঙে ফেলে, সমগ্র দেহে প্রীতির শিহরণ জাগায়, এবং যাহা মিলনের নাটকের প্রারম্ভিক অঙ্গভঙ্গির সদৃশ।
ণিঅআণুমাণ ণীসঙ্ক হিঅঅ দে বিরম এত্তাহে।
অমুণিঅ পরমত্ত্থ জণাণুলগ্গ কীস ম্হ লহুএসি॥ ৩৪৫
হে হৃদয়! তুমি কি কেবলমাত্র নিজের কল্পনালব্ধ সিদ্ধান্তে ভর করিয়া, যাহার প্রকৃত আন্তরিকতা অজানা, তদপির প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমাদেরকে কেন অপমানের পাত্র করিলে? বিরত হও।
অোসহিজ্-জণো পঈণা সালাহমাণেণ অই চিরং হসিও।
চন্দো ত্তি তুজ্ঝ ৱঅণে বিউণ্ণ-কুসুমঞ্জলি বিলক্খো॥ ৩৪৬
গৃহস্থ ব্যক্তি, যিনি গার্হস্থ্য-যজ্ঞে নিয়োজিত, তিনি যখন তোমার স্বামীর দ্বারা প্রশংসিত হইলেন, তখন দীর্ঘ সময়ব্যাপী হাস্যরসের বিষয় হইলেন। কারণ তিনি অজ্ঞাতবশে তোমার মুখমণ্ডলকে চন্দ্রমা ভ্রমণ করিয়া তাহাতে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিলেন।
পিশাচী অপভ্রংশ একটি তথাকথিত “ভ্রষ্ট” বা “অপভ্রষ্ট” রূপ, যাহা মূল সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ধ্বনিগত কাঠামো হইতে বিচ্যুত।পিশাচ ভাষা (গুণাঢ্য রচিত), যাহা মধ্যপ্রদেশ ও বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, প্রাকৃত-পরিবারভুক্ত, এবং পৈশাচী ভাষা বলিয়া চিহ্নিত।
গুণাঢ্য প্রসঙ্গে যাহা বলা হয় তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম রহস্যময় অধ্যায়। সাতবাহনরাজ-সম্বদ্ধে রচিত কথাসরিত্সাগর-এ গুণাঢ্য নামে এক কবির কথা পাওয়া যায়, যিনি একবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশী এই তিন ভাষা ত্যাগ করেন। পরিশেষে তিনি দেবীর আদেশে পিশাচী ভাষা গ্রহণপূর্বক বৃহৎকথা নামক এক অনুপম কাহিনিসমূহ রচনা করেন, যাহা পরে নানা অপভ্রংশ মার্গে ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যে প্রবাহিত হইয়াছে।
উক্ত শ্লোকপুঞ্জ সমেত ব্যাখ্যা নিম্নরূপে উপস্থাপিত হইতেছে—
तत स मर्त्यवपुषा माल्यवान्विचरन् वने ।
नाम्ना गुणाढ्यः सेवित्वा सातवाहनभूपतिम् ॥ १ ॥
সে মহাকবি গুণাঢ্য, যিনি মর্ত্যদেহধারী হইয়া মাল্যবান পর্বতে বিচরণ করিতেছিলেন, নামতঃ গুণাঢ্য নামে খ্যাত, পূর্বে সাতবাহন রাজাকে সেবা করিয়াছিলেন।
संस्कृताद्यास्तदग्रे च भाषास्तिस्रः प्रतिज्ञया ।
त्यक्त्वा खिन्नमना द्रष्टुमाययौ विन्ध्यवासिनीम् ॥ २ ॥
তিনি এক গভীর প্রতিজ্ঞা করিয়া সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশী এই ত্রৈধ ভাষা ত্যাগ করেন এবং তৎপরিনামে মানসিক ক্লেশভোগ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর দর্শনে গমন করেন।
तदादेशेन गत्वा च काणभूतिं ददर्श सः ।
ततो जातिं निजां स्मृत्वा प्रबुद्धः सहसाभवत् ॥ ३ ॥
দেবীর আদেশানুসারে তিনি কাণভূতি নামক এক পিশাচসদৃশ চরিত্র দর্শন করেন, ও তৎক্ষণাৎ নিজের পুরাতন জাতিস্মৃতি উপলব্ধি করেন।
आश्रित्य भाषां पैशाचीं भाषात्रयविलक्षणाम् ।
श्रावयित्वा निजं नाम काणभूतिं च सोऽब्रवीत् ॥ ४ ॥
তিনি ভাষাত্রয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, পিশাচী ভাষাকে অবলম্বন করেন, এবং কাণভূতিকে নিজের নাম শ্রবণ করাইয়া বলেন—
पुष्पदन्ताच्छ्रुतां दिव्यां शीघ्रं कथय मे कथाम् ।
येन शापं तरिष्यावस्त्वं चाहं च समं सखे ॥ ५ ॥
“হে বন্ধু! পুষ্পদন্ত হইতে শ্রুত যে দিব্যকথা আছে, তাহা আমাকে ত্বরায় কহ, যেন আমরা উভয়ে অভিশাপ অতিক্রম করিতে পারি।”
तच्छ्रुत्वा प्रणतो हृष्टः काणभूतिरुवाच तम् ।
कथयामि कथां किं तु कौतुकं मे महत्प्रभो ॥ ६ ॥
এই শুনিয়া কাণভূতি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নম্রভাবে বলেন, “হে প্রভু! আমি কাহিনী বলিব, কিন্তু তাহাতে আমার এক বৃহৎ কৌতূহল রহিয়াছে।”
এইরূপে, গুণাঢ্য প্রথাগত ভাষা ত্যাগ করিয়া পিশাচী ভাষায় বৃহৎকথা রচনা করিলেন, যাহা পরবর্তী কালে অপভ্রংশ মার্গে রূপান্তরিত হইয়া পাঞ্জাবি, লাহণ্ডা, সারায়িকি প্রভৃতি ভাষার আদি ভিত্তি রচনা করিল। পিশাচী অপভ্রংশ হইতে এই অঞ্চলের লোকভাষা বিকশিত হইয়াছে, ইহাই ভাষাতত্ত্বের এক ঐতিহাসিক প্রমাণ।
এইভাবে, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্ট এবং সেখান হইতে আঞ্চলিক ভাষাসমূহে ধ্বনিগত ও ব্যাকরণগত রূপান্তরের এক সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক পরম্পরা নির্মিত হইয়াছে, যাহার মূলে আছে ইতিহাস, ধর্ম, নাট্যকলার বিকাশ এবং জনসমাজের মুখের ভাষার ধারা।
Read Also
হিন্দী ভাষার উৎস ও বঙ্গভাষার সহিত প্রাচীন ঐতিহাসিক সংযোগ