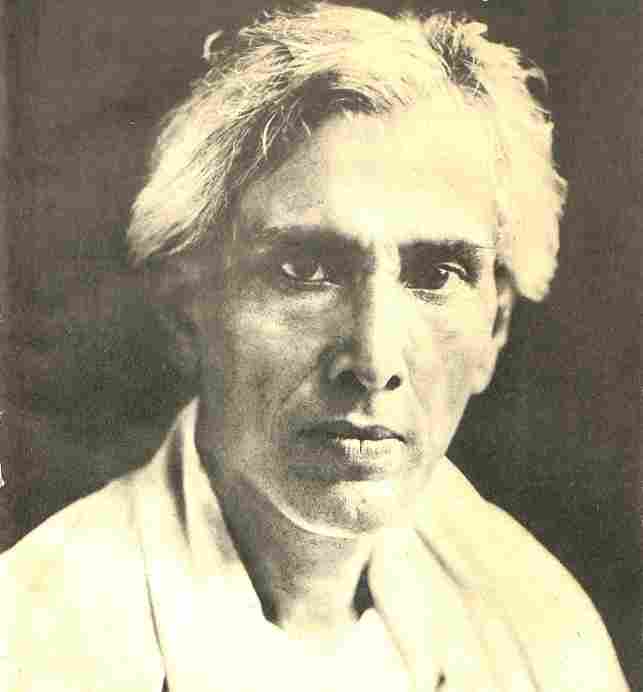কাব্য মীমাংসা: কবিরাজ রাজশেখর (850-900 খ্রি.)
রাজশেখরকৃত কাব্যমীমাংসা-য় শব্দ, অর্থ, অলংকার, রস ও শাস্ত্রকবিতার বিশদ বিচার
রাজশেখর-রচিত কাব্যমীমাংসা গ্রন্থের “কবিরহস্য” পরিচ্ছেদের প্রথম আলোচনায় ‘ব্যুত্পত্তি’ ও ‘কবিপাক’-এর ব্যাখ্যা নিয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—
পণ্ডিতদের মতে, ব্যুত্পত্তি আর কবিপাক (व्युत्पत्ति-कविपाकाः) দুইয়েরই তাৎপর্য বিশদ জানা যায়। আচার্যগণ বলেন: “ব্যুত্পত্তি” মানে হচ্ছে ভাষার এমন প্রশিক্ষণ, যা কবির কথা সর্বদিক থেকে প্রসারিত হতে সক্ষম হয়।
তাই বলা হয়েছে:
কোনও বিশেষ অনুশীলন ছাড়াই যে বাক্য সর্বদা বিস্তৃত হয়, তা তো কারও চোখে পড়ে না। আসলে সেটাই কবিত্ব, যখন বাক্য সর্বদিকপ্রসারী হয়।
একজন মতপ্রবক্তা বলেছেন— “যথোচিত ও অযথোচিত বিষয়ে বিচার করার ক্ষমতাই ব্যুত্পত্তি।”
আনন্দ নামক আরেকজন বলেন— “ব্যুত্পত্তি থাকলেও তার চেয়ে প্রতিভা শ্রেষ্ঠ।” কারণ প্রতিভা এমন শক্তি, যা কবির ব্যুত্পত্তির অভাবে যে সকল ত্রুটি হয়, সেগুলিকে ঢেকে দেয়।
এই বিষয়ে বলা হয়েছে—
“ব্যুত্পত্তির অভাবে কবির যে দোষ জন্মায়, কবির শক্তি তা ঢেকে দিতে পারে। তবে যদি সেই দোষ অশক্তির দ্বারা জন্মায়, তা হলে তা ঢাকাই যায় না, প্রকাশ পেয়েই থাকে।”
এখানে ‘শক্তি’ শব্দটি রূপক অর্থে প্রতিভা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
যেমন বলা হয়েছে—
“এটা কী আমার পিতার মাথায় স্থিত? এটা কী অমৃত-জনিত খণ্ড? এটি কী ললাট? এটি কী চোখ? হাতে কি সাপ?—
এভাবে ক্রোঞ্চরিপু (শিব) যখন দিক্বস্ত্রধারী অবস্থায় ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন দেবীর বাঁহাত উপরে রেখে যে হাসি প্রস্ফুটিত হল, তা আপনাদের রক্ষা করুক।”
অর্থাৎ, শৈল্পিক প্রশ্নের মধ্যে এমন প্রতিভার প্রকাশ ঘটে।
এবার মঙ্গল বলেন— “ব্যুত্পত্তিই শ্রেয়।”
কারণ ব্যুত্পত্তি থাকলে কবির অশক্তির দ্বারা যে দোষ জন্মায়, তাও ঢেকে যেতে পারে।
যেমন বলা হয়েছে—
“ব্যুত্পত্তি দ্বারা কবির অক্ষমতা আচ্ছাদিত হয়, কাব্যের পথে। রুচিশীল ব্যক্তিদের কাছে নিন্দনীয় শব্দগুচ্ছের রচনাও তখন গৃহীত হয়।”
ব্যুত্পত্তির একটি উদাহরণ—
“গলায় নেই কণ্ঠহার, তবুও যেন কণ্ঠজুড়ে উজ্জ্বলতা; দেহে নেই সোনার চুড়ি, তবুও যেন কৃশ লতার মতো। কানে রাখা নেই কুন্ডল, তবুও যেন শোভিত। বস্ত্রও নয় সুপরিচ্ছন্ন রেশম, তবুও যেন শুভ্র ও সৌম্য। প্রেমলীলা-আসনে আসীন নারী তখন এমন এক অপূর্ব দৃশ্য।” (व्युत्पत्तिर्यथाऽकृतः कण्ठे निष्को नहि किमुत तन्वी मणिलता कृशं लीलापत्रं श्रवसि निहितं कुण्डलम्रचि ।
न कौशेयं चित्रं वसनमवदातं तु वसितं समासन्नीभूते निधुवन विलासे वनीतया ।।)
এরপর বলা হয়েছে— “প্রতিভা ও ব্যুত্পত্তি যখন উভয়ে যুক্ত হয়, তখন তা সর্বোত্তম।”
যেমন রূপ ও সৌন্দর্যের মধ্যে লাবণ্য আর রূপ আলাদা হলেও, এই দুইয়ের মিলনে পরিপূর্ণতা আসে।
দুইয়ের যুগল দৃষ্টান্ত—
“যার জঙ্ঘা, উরু ইত্যাদি অঙ্গ নখের আলোয় দীপ্তিমান, লাল আলক্তক রাঙা, পদ্মকলিকার মতো, মঞ্জীরঘণ্টার ধ্বনি সঙ্গে রেখে নিজের দেহের স্বচ্ছ লাবণ্য থেকে উৎপন্ন হওয়া পুকুরের মতো কমলফুলের শোভা নিয়ে, দেবী ভবানীর নবীন দণ্ডপাদ (পা) নৃত্যের অনুকরণে বিজয়ী হয়ে উঠেছে।” (यथा- ऽजङ्घाकाण्डोरुनाले नखकिरणलसत्केसरासीकरालः प्रत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मञ्जुमञ्जीरभृङ्गः । भर्त्तुर्नृत्यानुकारे जयति निजतनु स्वच्छ लावण्यवापी-सम्भूताम्भोज शोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याःऽ)
এমন প্রতিভা ও ব্যুত্পত্তি যাঁর মধ্যে থাকে, তিনিই প্রকৃত কবি।
এবং কবি তিন প্রকার—
(১) শাস্ত্রকবি, (২) কাব্যকবি, (৩) উভয়কবি।
শ্যামদেব বলেন— “এদের মধ্যে উভয়কবি শ্রেষ্ঠ।”
কিন্তু অন্যজন বলেন— “না, প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। যেমন রাজহংস চাঁদের আলো পান করতে পারে না, আবার চকোর পাখি জল থেকে দুধ আলাদা করতে পারে না।”
শাস্ত্রকবি যখন কাব্যের রসবন্ধন নষ্ট করেন, তখন তিনি একরকম। আর কাব্যকবি যখন কঠিন শাস্ত্রকথাকেও কবিত্বের অলংকারে নরম করেন, তখন আরেকরকম। উভয় কবি যখন দুই দিকেই পারদর্শী হন, তখন তিনিই সবার থেকে বড়।
তবে শাস্ত্র ও কাব্য দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য আছে।
শাস্ত্রের সংস্কার কাব্যকে সাহায্য করে, কিন্তু একপাক্ষিক শাস্ত্রনিষ্ঠতা কাব্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবার কাব্যের সংস্কার শাস্ত্রবাক্যের রস বৃদ্ধি করে, কিন্তু শুধু কবিতা নিয়ে থাকলে শাস্ত্রের গভীরতা হারায়।
শাস্ত্রকবি আবার তিন রকম—
(১) যে শাস্ত্র রচনা করেন, (২) যে শাস্ত্রে কাব্যরস আনেন, (৩) যে কাব্যে শাস্ত্রতত্ত্ব আনেন।
কাব্যকবি আট প্রকার—
(১) রচনাকবি, (২) শব্দকবি, (৩) অর্থকবি, (৪) অলংকারকবি, (৫) উক্তিকবি, (৬) রসকবি, (৭) মার্গকবি, (৮) শাস্ত্রার্থকবি।
এর মধ্যে রচনাকবির একটি উদাহরণ—
“লোলাট লতার মতো লেজ দোলানো গন্ধবাহ নামে যে বাতাসী, তারা যখন ঝর্ণার গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, শুষ্ক গাছের শাখা ঝুলিয়ে, বিশাল বিষধরদের মতো সমুদ্রতীরে তরঙ্গ ভেঙে পড়ছে। সেই সময় গাছের পাতা খসে পড়ছে, সবই সেই কবির বর্ণনায় উঠে আসে।”
শব্দকবিরও তিন প্রকার, নামকবি, আখ্যাতকবি এবং নাম-আখ্যাতকবি।
নামকবির উদাহরণ:
“যেমন অজ্ঞতা পুরুষের জন্য, মহিমা রাজার জন্য, জ্ঞান চিকিৎসকের জন্য, দয়া সাধুর জন্য, লজ্জা বীরের জন্য, সৌন্দর্য যুবকের জন্য অলংকার হয়, তেমনি শব্দই রাজার অলংকার।”
আখ্যাতকবির উদাহরণ:
“জোরে জোরে হাসল, আনন্দে কেঁপে উঠল, বজ্রধ্বনি তুলল বাহু-তটিনীর দ্বারা কম্পিত হয়ে, প্রশংসা করল, সুখী হল, গুরুজনের বাক্যে অমৃত লাভের আশ্বাস পেয়ে।”
নাম-আখ্যাতকবির উদাহরণ:
“আলোহীন, শক্তিহীন বাহু, নারীরা যেন বিষাদের দ্বারা অচেতন, না কাঁদল, না চিত্কার করল, না শব্দ তুলল, না চলল, প্রাণহীন প্রতিমূর্তির মতো মুহূর্তকাল স্থির থাকল।”
অর্থকবি:
“দেবী জন্ম দিলেন পুত্রকে। গনগণ নৃত্য করতে লাগল। ‘কী দাঁড়িয়ে আছ?’ — এই কথা বলে ব্রহ্মা-শক্তির দ্বারা উত্সাহিত চামুণ্ডা তাকে আলিঙ্গন করলেন। আপনাদের রক্ষা করুক সেই দৃশ্য যেখানে দেবদুন্দুভির ধ্বনি ছাপিয়ে একে অপরের অঙ্কে পতন করে দুই দেবতা এমন শব্দ তুললেন, যেন জরা-পীড়িত স্থূল অস্থির ভাঙা আওয়াজ।”
আলংকারিক কবি দুই প্রকার: শব্দ অলংকার এবং অর্থ অলংকার।
শব্দ অলংকারের উদাহরণ:
“পূর্বাহ্নে বিষ পান, পূর্বাহ্নে পাপের ফলে বিষ পান, মৃত্যু হলে গঙ্গায় মরেছি কিনা, দুর্ভাগ্যবশত রাজপথে মরেছি।”
অর্থ অলংকারের উদাহরণ:
“ভুল করা জিহ্বার পতাকা, ফণার ছায়া, বসুকীর, দংশনের কাঁটায় বিদীর্ণ — এমনটি করার উপযুক্ত আমার বাহু।”
উক্তিকবি উদাহরণ:
“এই পেট, এই সুন্দরী মহিলার শ্বাসপ্রশ্বাসের তরঙ্গ, স্তনের পরিধির সীমা পর্যন্ত বাহু-লতার লেহনযোগ্য, মুখের চন্দ্র সদা স্পন্দিত, বাক্যরস ধারায় পানযোগ্য, এই সব যুবতীর যৌবনের খেলা।”
অথবা:
“আশোক গাছের কিশলয় অনীহার মতো ঠোঁট ঘুরে দাঁড়ায়, গাল পাণ্ডুর হয়ে পড়ে, তালে তালে পড়ে যায়। চোখ পদ্মিনীকে স্মরণ করায় শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম। এভাবেই কোমলতা ও মাধুর্য স্পর্শ করে এবং দেহ স্নিগ্ধ হয়।”
রসকবি উদাহরণ:
“তাম্রপত্রী নদী দেখে তুমি বিস্মিত হয়ো না, তার মধ্যে মুক্তার খোল খুলে গহনা-মূর্ত রূপে যা বের হয়, তেমনই তা। সেই জলের ফেনা ভ্রুকুটির নারীসৌন্দর্য হয়ে স্তনের মধ্যে পরিণত হয়।”
মার্গকবি উদাহরণ:
“মূল নেই এমন তরুণ কীর্তির বৃক্ষ, সুবাসিত জাতীর পাতা, চন্দনের চাঁদের মতো সরল কিশলয়, কোমল অশোক পাতার মতো; শিরীষ ফুলের গন্ধময়তা, মুক্ত ফল ধরা ইত্যাদি; এই সব একত্রে গ্রীষ্মে যে দাহ শান্ত করে, তা পূর্বে গ্রীষ্মপঞ্চক নামে বিখ্যাত ছিল।”
শাস্ত্রার্থকবি উদাহরণ:
“যারা অন্তরে আনন্দিত, কর্মত্যাগে নিপুণ, নির্লিপ্ত সমাধিতে অবিচল, জ্ঞানের উত্থানে অন্ধকার মোচন করেছেন, যারা সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, তারা এমন একটিকে দর্শন করেন যিনি আলোকেরও অতীত, অন্ধকারেরও অতীত। যে ব্যক্তি মোহান্ধ, সে এই পুরাতন দেবতাকে কেমন করে চিনবে?”
এদের মধ্যে যাঁর দুই বা তিনটি গুণ আছে, তিনি মধ্যম; পাঁচটি গুণ থাকলে তিনি উত্তম; আর সব গুণ থাকলে তিনি মহাকবি।
কবির দশটি অবস্থা বা স্তর:
(১) কাব্যবিদ্যা-স্নাতক (काव्यविद्यास्नातक), (২) হৃদয়কবি, (৩) অন্যাপদেশী, (৪) সেবিতা, (৫) ঘটমান, (৬) মহাকবি, (৭) কবিরাজ, (৮) আওয়েশিক, (৯) অবিচ্ছেদী, (১০) সংক্রাময়িতা।
যিনি কবিত্বের ইচ্ছায় কাব্যবিদ্যা অর্জনের জন্য আচার্যের কাছে যান, তিনিই কাব্যবিদ্যা-স্নাতক।
যিনি হৃদয় থেকেই কবিতা করেন, তিনি হৃদয়কবি।
যিনি নিজের কবিতা অন্যের নামে পড়ে শোনান, তিনি অন্যাপদেশী।
যিনি পূর্বপুরুষদের ধারা ধরে রাখেন, তিনি সেবিতা।
যিনি নির্দোষ কবিতা রচনা করেন কিন্তু বহু লিখতে পারেন না, তিনি ঘটমান।
যিনি কোনও একটি ধারায় পারদর্শী, তিনি মহাকবি।
যিনি বিভিন্ন ভাষা, প্রবন্ধ এবং রসে দক্ষ, তিনি কবিরাজ।
যিনি মন্ত্র বা শিক্ষার দ্বারা সিদ্ধি পেয়ে একদম সমকালে কবিতা রচনা করেন, তিনি আবিশিক (आविशिकः)।
যিনি যখন ইচ্ছা তখন নিরবিচারে কবিতা রচনা করেন, তিনি অবিচ্ছেদী।
যিনি সাধিত মন্ত্র দিয়ে সরস্বতীর অনুগ্রহ অন্যদের মধ্যে প্রবাহিত করেন, তিনি সংক্রাময়িতা।
সতত অনুশীলনে কবির বাক্য পাক হয়।
এই পাক কী? আচার্যগণ বলেন, ‘পরিণতি।’
এই পরিণতি কী? মঙ্গল বলেন: ‘অব্যাহত শব্দ ও অর্থের শ্রুতি।’ অর্থাৎ শব্দভঙ্গি সুন্দর হওয়া।
আচার্যগণ বলেন: ‘শব্দের স্থিতি ও স্থৈর্যই পাক।’ যেমন বলা হয়েছে—
“যতক্ষণ মন দোলায়, ততক্ষণ শব্দ স্থির হয় না। যখন শব্দ স্থিত হয়, তখন সরস্বতী সিদ্ধ হন (सिद्धा सरस्वती)।”
বামনীয়গণ বলেন:
“শব্দ যখন নিজ নিজ স্থানে স্থিত হয়, তখনই সেটাই পাক (शब्दपाकं )।”
অন্তঃস্থভাবে ব্যাখ্যা: এটা কেবলমাত্র অক্ষমতা নয়, বরং উচ্চস্তরের শব্দ ও অর্থের সংযোজনে গঠিত রসসম্মত বাক্যই পাক।
এই কারণেই বলা হয়েছে—
“গুণ, অলংকার, রীতি, শব্দার্থের বিন্যাস যার দ্বারা রসিকদের জিভে স্বাদ হয়, সেটাই বাক্যের পাক।”
এছাড়াও বলা হয়েছে:
“যখন বক্তা, অর্থ, শব্দ, রস—সবই ঠিক থাকে, তখনই বাক্যের মধ্যে মৌচাকের মতো মধু প্রবাহিত হয়।”
तदुक्तम्ऽसति वक्तरि सत्यर्थे शब्दे सति रसे सति । अस्ति तन्न विना येन परिस्त्रवति वाङ्मधु
অতএব, এই পাক শ্রোতারা অনুভব করেন, এটি এক ধরনের সাহিত্যিক ব্যবহারের অঙ্গ।
কবিগ্রামে অর্থাৎ কবির সমাজে, কাব্য ন’ভাবে পাক হয়—
(১) শুরু ও শেষে অস্বাদু—পিচুমন্দ-পাক,
(২) শুরুতে অস্বাদু, শেষে মাঝারি—বদর-পাক,
(৩) শুরুতে অস্বাদু, শেষে স্বাদু—মৃদ্বীকা-পাক,
(৪) শুরুতে মাঝারি, শেষে অস্বাদু—বার্তাক-পাক,
(৫) শুরু ও শেষে মাঝারি—তিন্তিড়ীকা-পাক,
(৬) শুরুতে মাঝারি, শেষে স্বাদু—সহকার-পাক,
(৭) শুরুতে উত্তম, শেষে অস্বাদু—ক্রমুক-পাক,
(৮) শুরুতে উত্তম, শেষে মাঝারি—ত্রপুস-পাক,
(৯) শুরু ও শেষে স্বাদু—নারিকেল-পাক।
প্রথম তিনটি পরিত্যাজ্য।
ভালো কবি হোক, কিন্তু খারাপ কবি না। খারাপ কবিতা হলো মৃত্যুর মত (वरमकविर्न पुनः कुकविः स्यात् । कुकविता हि सोच्छ्रवासं मरणम् ।)। মাঝারি কবি সংস্কারযোগ্য। যেমন অপরিশুদ্ধ সোনা আগুনে শুদ্ধ হয়।
শ্রেষ্ঠ কবিতার আর সংস্কার প্রয়োজন হয় না। যেমন মুক্তা ঘষা-মাজার প্রয়োজন করে না।
অপরিকল্পিত পাককে ‘কপিত্থ-পাক’ বলে। যেমন ধান ছেঁড়া হলে অন্নকণা পাওয়া যায়, তেমনই মাঝে মাঝে সুভাষিত বাক্য পাওয়া যায়।
যে ব্যক্তি কাব্যশাস্ত্রকে ভদ্রভাবে অধ্যয়ন করে, তার কবিতা নয় প্রকারে পরিপক্ক হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি হান-উপাদান সূত্র (हानोपादानसूत्रेण) অনুসারে এগুলিকে ভাগ করে নেন।
এইসব নিয়ম শিষ্যদের দেখানো হয়েছে। তবে জগতে এর বৈচিত্র্যও আছে।
রাজশেখরকৃত কাব্যমীমাংসায় কবিত্বের শ্রেণিবিন্যাস ও ধাপসমূহ
বাংলা অনুবাদ: তন্ময় ভট্টাচার্য (অ্যাডভোকেট)
শৃঙ্গাররসের শ্রেষ্ঠত্ব: শ্রীভোজদেবকৃত শৃঙ্গারপ্রকাশের আলোকে